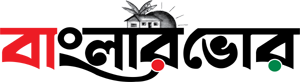অধ্যাপক মো: ছোলজার রহমান
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নবীন পলল গঠিত মৃতপ্রায় ও সক্রিয় বদ্বীপ নিয়ে গঠিত ভূ-ভাগ। এর উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশে বদ্বীপ গঠণ প্রক্রিয়া প্রায় স্তিমিত হয়েছে- যাকে মৃতপ্রায় বদ্বীপ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশে পলল সঞ্চয় ও ভূগঠণ এখনও চলমান-যাকে সক্রিয় বদ্বীপ বলা হয়। এছাড়াও নদীবাহিত পলল ও ঘূর্ণিঝড় তাড়িত সামুদ্রিক পলল সঞ্চয়ের ফলে দক্ষিণাংশে নতুন ভূ-ভাগ গঠিত হচ্ছে এবং সমুদ্র উপকূলরেখা ও সুন্দরবন ক্রমশ: দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। ৪/৫ শত বছর আগে এ অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকা গভীর জলাভূমিরুপে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত জোয়ার-ভাটার প্রভাবযুক্ত ছিল। স্টিমার ও লঞ্চ এ অঞ্চলের সকল জেলা ও উপজেলার জলাভূমি,খাল ও নদীসমূহ দিয়ে চলাচল করত এবং যাতায়াত ও পরিবহণেজলযানের প্রাধান্য ছিল। জমিসমূহ প্রাকৃতিকভাবেই বেশ উর্বর ছিল, শিল্পে অনগ্রসর এবং জনসংখ্যা কম ছিল, উদ্ভিজ্জ ও জলাশয়ের পরিমাণ বেশি ছিল- মৃত্তিকা-পানি-বায়ুদূষণ-শব্দদূষণ হতো না বললেই চলে। ৬০-৭০ বছর আগেও এখানকার তাপমাত্রা কখনও সর্বোচ্চ কিংবা সর্বনিম্ন হতো না, অনেকটাই আরামদায়ক ছিল। এ অঞ্চলের নদীনালার পানিপ্রবাহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বগামী ছিল।
১৮৬০ এর দশকে কলকাতা থেকে দর্শনা হয়ে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম রেললাইন স্থাপনের কাজ শুরু হলে এ অঞ্চলের সকল নদী ও জলাভূমিসমূহ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়। এতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ থেকে নদীবাহিত পললের আগমন বন্ধ হয়ে যায় এবং ভূগঠণ, নদীপ্রবাহ, পানিচক্র, মৎস সম্পদ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। মিঠা পানির পরিমাণ ও প্রবাহের গতিবেগ কমে যাওয়ায় সামুদ্রিক লবণাক্ত পানি ও লবণাক্ততা এ অঞ্চলের অনেকটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মাটির গুণাগুণ, উর্বরতা ও ফসল উৎপাদনকে ব্যহত করে। ১৯৭০ এর দশকে পদ্মা নদীর উপর ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে পানি প্রত্যাহার ও ভিন্ন নদীখাতে পানি প্রবাহিত করায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের শাখানদীসমূহের পানি প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং পলল সঞ্চয়, ভূগঠণ, উর্বরতা, মৎস সম্পদ, লবণাক্ততা, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং ক্রমশ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অঞ্চলটিতে পলল সঞ্চয় ও ভূগঠণ না হওয়ায় এবং দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকাসমূহ সামুদ্রিক পলল সঞ্চয়ের ফলে কিছুটা উঁচু হতে থাকায় এখানকার জলাভূমি ও নিম্নভূমিসমূহে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ফরিদপুরের দক্ষিণভাগ থেকে পূর্বাঞ্চলের নদ-নদীসমূহের প্রবাহ পথ দক্ষিণ-পশ্চিমগামী হতে থাকে। ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক উঁচু হতে থাকে এবং যশোর-নড়াইল-খুলনা-সাতক্ষীরা এর মধ্যবর্তী একটি বৃহৎ ভূভাগে জলাবদ্ধতার প্রকোপ দেখা দেয়, লবণাক্ততাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অঞ্চলের নদীসমূহে পানিপ্রবাহ কমতে থাকে এবং বছরের পুরো সময় পানি থাকে না। ফলে এক বড় অংশে মৃত্তিকা আর্দ্রতা, উর্বরতা, মিঠা পানির প্রাকৃতিক মৎস, প্রতিবেশ ব্যবস্থা হ্রাস পেতে থাকে। নদীসমূহ ক্রমাগত দখল হয়ে ভূমি জরিপের সময় ব্যক্তির নামে রেকর্ড করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হতে থাকে এবং মৃত নদী ও অপ্রশস্ত খালে পরিণত হয়। দূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যভাগের এ বিস্তৃত এলাকাটি একটি বৃহৎ বাটি বা গামলা সদৃশ অভ্যন্তরীণ নিম্নভূমির জলাশয় বা হ্রদে পরিণত হবে যেখানে ভূমির ঢাল হবে সকল দিক থেকে ভিতরের দিকে নিম্ন বা কেন্দ্রগামী। এ জলাশয়ের পানি সামান্য লবণাক্ত হবে এবং একটা সময় এ স্থান থেকে পানি প্রবাহ বাইরের দিকে মোটেও প্রবাহিত হবে না বরং চতুর্দিকের পানি প্রবাহের জন্য মোহনার আকার ধারণ করবে এবং ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু পললমুক্ত স্বাদু পানি কোন না কোন পথে সোজা দক্ষিণ বরাবর কিংবা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হবে। চতুর্দিক থেকে আগত এসব পানির প্রবাহ যদি কোন বড় নদী থেকে আসে তবে সে পানির সাথে বাহিত পলি সঞ্চিত হয়েই কেবল এ এলাকার জলাবদ্ধ দশার নিরসন করতে সক্ষম হবে এবং এরুপ অবস্থা আসতেও অনেক বছর প্রয়োজন হবে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের খ্যাতনামা পানি বিজ্ঞানীদের মতামতের ভিত্তিতে গঠিত বেশ কয়েকটি মিশন এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনের কর্মসূচী অনেক বছর থেকে পরিচালনা করে অনেক অর্থ ব্যয় করেছে। সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে অনেকগুলো পোল্ডারে ভাগ করেও চেষ্টা চালানো হয়েছিল। সাময়িকভাবে পোল্ডারের অভ্যন্তরভাগের এলাকাকে সামুদ্রিক জোয়ারের লবণাক্ত পানি থেকে রক্ষার মাধ্যমে এলাকাবাসী ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত ভালো ফসল পেয়েছিল। তার কয়েক বছর পরে দেখা গেল যে সামুদ্রিক পলল পোল্ডারের বেষ্টনির বাইরে উঁচু হয়ে গঠিত হয়েছে এবং পোল্ডারের অভ্যন্তরভাগের জমিসমূহ বেশ নীচু রয়েছে। এই নীচু ভূভাগে বৃষ্টি ও বন্যার পানি জমলে তা আর বেরুতে পারে না এবং জলাবদ্ধতার উৎপত্তি হয়। পোল্ডার হলো মাটি দিয়ে তৈরি একটি গোলাকার বাঁধ যা একটি বড় এলাকাকে বেষ্টন করে রেখে বাইরে থেকে ভিতরে পানির প্রবেশকে বাঁধা দেয়, ফলে ভিতরে জোয়ারের লবণাক্ত পানি আসতে পারেনি এবং ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। ২০-২৫ বছরের ভালো ফসলের আশায় ভেবে দেখা হয়নি যে বাইরের ভূভাগ উঁচু হলে ভিতরের নিম্নভূমির কি অবস্থা হবে। ঠিক যেন ঢাকা শহরের ভবনসমূহের গঠণের মতো; চোর-ডাকাত-ধুলাবালি ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য মজবুত লোহার গ্রীল ও কাঁচ দিয়ে ঘিরে নিরাপদ করা হয় কিন্তু ভেবে দেখা হয়না যে ভিতরে আগুন লাগলে নিজেরা কিভাবে বেরুবে? পরবর্তীতে স্লুইস গেট পদ্ধতির মাধ্যমে ভিতরের পানি বের হবার ব্যবস্থা করা হলো এবং এর গেটসমূহ জোয়ারের পানি এলে বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে গেটসমূহের বাইরে জোয়ারের সাথে বাহিত পলি সঞ্চয় হয়ে উঁচু হতে থাকে এবং কয়েক বছর পর থেকে সেগুলো দিয়ে ভিতরের পানি বের হতে পারে না। ফলে বিপুল অর্থ ব্যয় করেও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান ও সুফল পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশ আমলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে অনেক অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প নেয়া হয়েছে। স্লুইস গেটের পশ্চাতের পানি নির্গমন পথ খনন, গ্রামভিত্তিক জোয়ারাধার তৈরি এখনও চলমান যা সামুদ্রিক জোয়ারের পানির সাথে পলল আসার ও ভূগঠণের একটি ধীর গতির প্রক্রিয়া। নদী ও খালসমূহ পানি প্রবাহের জন্য খনন করা হলেও খননকৃত মাটিসমূহ তার দুপাড়ে বেশ উঁচু করে জমিয়ে রাখা হয় এবং বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তা সে খাল বা নদীতে নেমে পুনরায় ভরাট করে ফেলে, তাই এ প্রক্রিয়ায় ২/১ বছরের জন্য সুফল পাওয়া যায়। জোয়ারাধার প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জমিতে ফসল ফলানোর কার্যক্রম বন্ধ থাকে, জমির মালিকদের নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং প্রকল্প ব্যয় অনেক হয়ে থাকে।
পশ্চিমাংশের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কপোতাক্ষ,নবগঙ্গা,চিত্রা, ইছামতি, মধুমতি, কুমার নদীসমূহের মাধ্যমে পদ্মা নদী এবং বৃষ্টিপাতের পানি এ অঞ্চলের অন্যান্য নদী ও খালসমূহের পানি প্রবাহের উৎস। এসব নদী থেকে প্রাপ্ত পানির মাধ্যমে সচল থাকে মুক্তেশ্বরী, বেত্রাবতি, কাজলি, ভদ্রা, হরিহর, ময়ূর প্রভৃতি নদী যা বর্তমানে প্রায় মৃত। ১৯৮০ এর দশক থেকে এসব নদীতে বাঁধ বা আইল দিয়ে নিজেদের/ব্যক্তিগত পুকুরে পরিণত করে ও পাটা দিয়ে মাছ চাষ ক্ষমতাশালীদের একটি নিয়মিত অধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চলে আসছে। স্থানীয় জেলে, মৎসজীবি ও জনগণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস আহরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, জলজ জীবের বিস্তার, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি হ্রাস পায়। সরকারি খাল, জলাশয়, নদী ও খাসজমিসমূহ দীর্ঘকাল যাবৎ সরকার পরিবর্তনের সাথে দখলদার ও ভোগকারির পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক আগাছানাশক, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং নগর ও শিল্পের বর্জ্য-রং-রাসায়নিকের একটি অংশ অঞ্চলের পানি ও মৃত্তিকায় মিশে মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ ঘটিয়ে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাখি ও জীববৈচিত্রের ক্ষতিসাধন করেছে এবং করেই চলেছে।
পরিবেশকর্মী, ভলান্টিয়ার, পরিবেশিক সংগঠণ,গণমাধ্যমকর্মী ও জনগণের একটি অংশ সক্রিয় থেকে মানববন্ধন, স্মারকলিপি ও প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে কোন কোনটিতে আংশিকভাবে সফল হতে পেরেছিল। অঞ্চলের অনেক নদীকে খননের মাধ্যমে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। খুলনা-যশোর-ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়ক, যশোর-নড়াইল, যশোর-চৌগাছা সড়কের গাছসমূহ একসাথে নিধন করায় ব্যাপকভাবে পরিবেশিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। গ্রামীণ রাস্তার ধারে বনায়নকৃত গাছসমূহের বাকল কেটে রেখে ও রাসায়নিক প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে মেরে ফেলা হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারি পুকুর সমূহের প্রায় সবই বন্ধ করা হয়েছে, বিদ্যমানগুলোতে পলিথিন ও বর্জ্য জমেছে। নদী ও মহাসড়কের পাশে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা রেখে স্থাপনা তৈরির বিধান মানা হচ্ছে না।
যশোরের ভৈরব নদী থেকে স্থায়ী ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলন দীর্ঘদিন চলমান থাকায় ঘোষপাড়ায় বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়া শুরু হয়েছে। মোল্লাপাড়ায় মাদ্রাসার নিকট থেকে ও কাজীপাড়া তেতুলতলার নিকট থেকেও বালু উত্তোলন করা হয়েছে, অভ্যন্তরের লালদীঘিকে সংকুচিত করা হয়েছে। চৌগাছা থেকে বুকভরা বাওড় পর্যন্ত ৩৬০ মৌজার পানিপ্রবাহকে বাঁধা দিয়ে পুকুর বানানো ও পাটা দিয়ে প্রাকৃতিক মাছের বংশবৃদ্ধি প্রতিহত করা হয়েছে। মুক্তেশ্বরী নদীর উৎসমুখ বেঁধে দিয়ে ফসলি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। অববাহিকার আকার ও সম্ভাব্য পানির পরিমাণ বিবেচনা না করে অল্প ব্যয়ে ছোট ব্রীজ বা কালভার্ট তৈরি করেও কেউ বাহবা নিয়ে থাকেন- যা গোটা দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। আরো অনেক ক্ষতিকর পদক্ষেপ প্রকাশ্যে গ্রহণ করে পরিবেশকে ব্যাহত করা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে ব্যবস্থা না নিয়ে অনেক বছর পরে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে বাহবা নিয়ে থাকেন। প্রতিকার হিসেবে একটি আইন দরকার এবং সেটি হলো-পরিবেশের ক্ষতি করা এবং অন্যের ও খাসজমির বেদখল কালের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-কর্তৃপক্ষ-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তির সাথে ক্ষতিপূরণ প্রদানের হার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা।
লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।